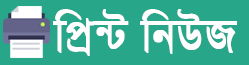নাগরিক মর্যাদা: বাংলাদেশে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা ও সম্ভাবনার নির্মোহ পর্যালোচনা / ইকবাল জিল্লুল মজিদ

নাগরিক মর্যাদা: বাংলাদেশে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা ও সম্ভাবনার নির্মোহ পর্যালোচনা
লেখক:
ইকবাল জিল্লুল মজিদ
পরিচালক, কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম
রাডডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টার, মিরপুর, ঢাকা
ভূমিকা
একটি রাষ্ট্রের সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি নির্ধারিত হয় তার নাগরিকদের মর্যাদা, সমান সুযোগ, ও সম্মানের নিশ্চয়তার মাধ্যমে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়ের অঙ্গীকারে। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় পরও প্রশ্ন থেকে যায়—এই রাষ্ট্রে নাগরিক মর্যাদা কি কেবল কাগজে-কলমে বন্দি এক ধারণা?
নাগরিক মর্যাদা: ধারণা ও প্রত্যাশা
নাগরিক মর্যাদা বলতে বোঝায়—সব মানুষের জন্য সমান অধিকার, নিরাপত্তা, সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আইনের সমতা, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্য প্রবেশাধিকার। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।
বাস্তবতা: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা
বাংলাদেশে সমাজের এক বিরাট অংশ—যেমন হিজড়া, দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বেদে সম্প্রদায়, গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, দিনমজুর, রিকশাচালক কিংবা চা-বাগানের শ্রমিক—তাদের জন্য নাগরিক মর্যাদা এখনো এক দূরতম স্বপ্ন।
এই মানুষগুলোর বেশিরভাগই জন্মসূত্রে নাগরিক হলেও, সামাজিক স্বীকৃতি, রাষ্ট্রীয় সেবা এবং আইনি সুরক্ষা পেতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার। বহুক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ও অবজ্ঞাত—যেখানে ক্ষমতাবান শ্রেণির কাছে নাগরিক মর্যাদা একটি সুবিধা, প্রান্তিক জনগণের কাছে তা অনুপলব্ধ এক অধরা আদর্শ।
পেশার ভিত্তিতে বৈষম্য:
বাংলাদেশে মানুষের পেশাগত পরিচয় আজও একধরনের মর্যাদাবোধ বা অপমানের উৎস। চিকিৎসক, প্রকৌশলী কিংবা আমলাদের যেমন সম্মান ও সুবিধা মেলে, তেমনি রিকশাচালক, মেথর কিংবা দর্জিদের সম্মানহীন জীবন যেন সামাজিকভাবে অনুমোদিত। অথচ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের এই চালিকাশক্তিরা সেবাদানের অদৃশ্য বীর।
যেমন হতে পারতো:
একটি সত্যিকারের সমানাধিকারের রাষ্ট্রে—
সব পেশার মানুষের কাজকে মূল্য দেওয়া হতো।
প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত সুযোগ নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি থাকতো।
পরিচয়পত্র, ঠিকানা বা দলিল নয়—মানবিক মর্যাদা হতো নাগরিকতার প্রধান মানদণ্ড।
রাষ্ট্রীয় বক্তৃতায় নয়, বরং মাঠপর্যায়ে মর্যাদার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হতো।
নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে কী দরকার?
১. নীতির পুনর্বিন্যাস: মানবিক মর্যাদাকে মূল ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তা নীতির সংস্কার।
২. শিক্ষায় মূল্যবোধের পুনর্গঠন: সম্মান, সহমর্মিতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রেণিকক্ষে যুক্ত করা।
৩. অদৃশ্য শ্রমের স্বীকৃতি: গৃহশ্রম, পরিচ্ছন্নতাকর্ম, পথশিশুদের সংগ্রামকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় স্বীকৃতি দেওয়া।
৪. নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি: মর্যাদার ধারণা জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি, কারণ মর্যাদা শুধু দান নয়—দাবি।
৫. রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন: জাতীয় পুরস্কার, দিবস ও নীতিমালায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি।
পরিশেষে:
বাংলাদেশে নাগরিক মর্যাদার বাস্তবায়ন এখনো অসম্পূর্ণ ও বৈষম্যমূলক। অথচ এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার প্রতিটি নাগরিক—হোক তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কিংবা রাস্তার ঝাড়ুদার—তার মর্যাদাপূর্ণ বেঁচে থাকার সুযোগের উপর।
আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একটি মানবিক রাষ্ট্র গড়তে চাই, তবে নাগরিক মর্যাদা দিতে হবে কাজ, পরিচয় ও শ্রেণি-ধর্ম নির্বিশেষে।
রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তার মর্যাদার অনুভব থেকেই জন্ম নেয়। তাই এই মর্যাদাবোধের প্রসার ঘটানোই হবে একটি ন্যায্য ও সংহত বাংলাদেশের রূপরেখা।
সংগ্রহ - আমির হোসেন
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত