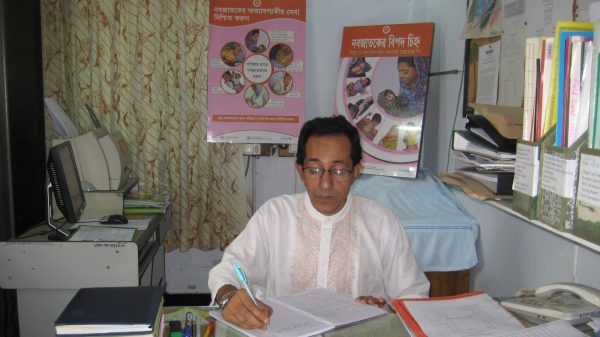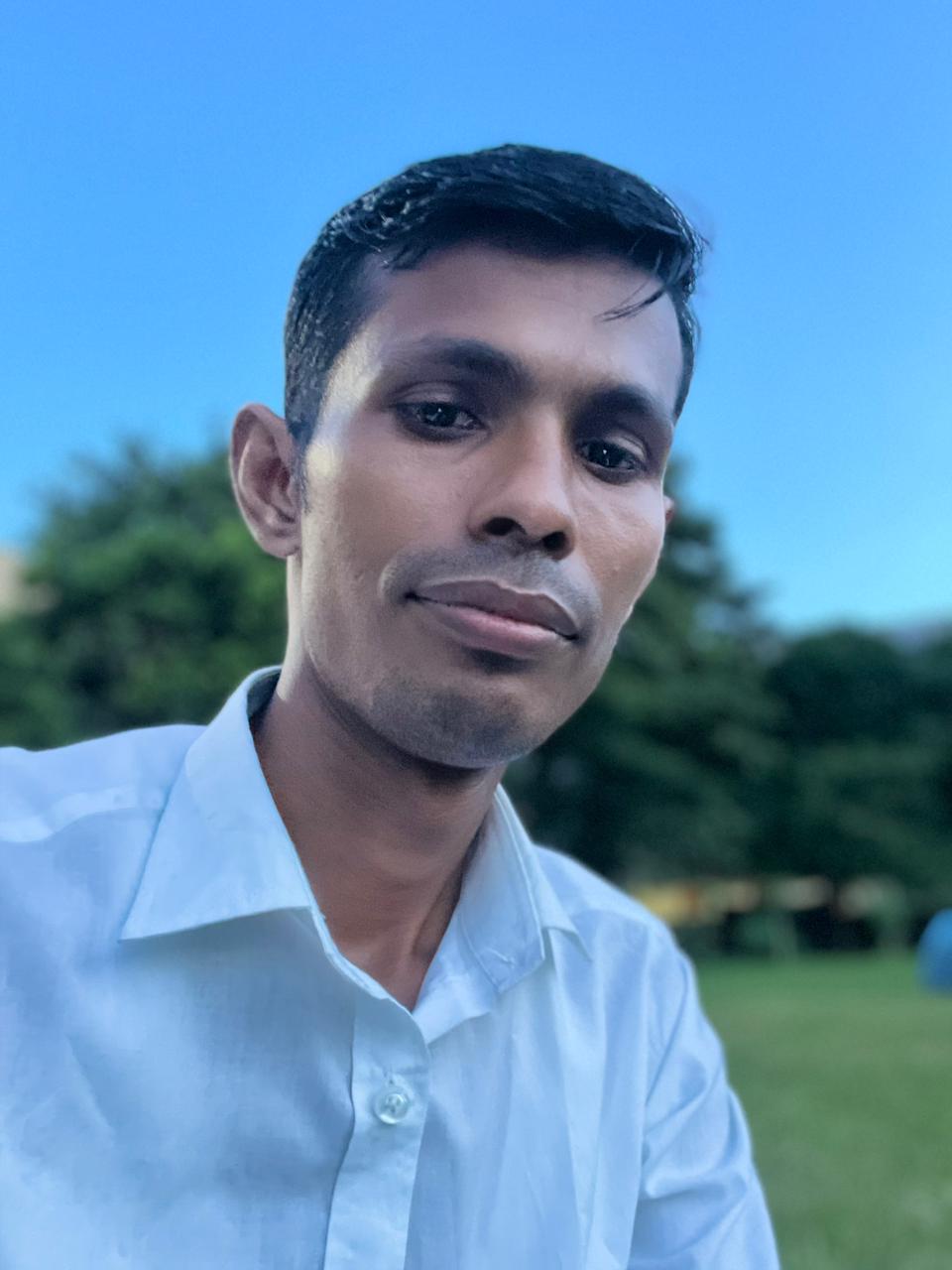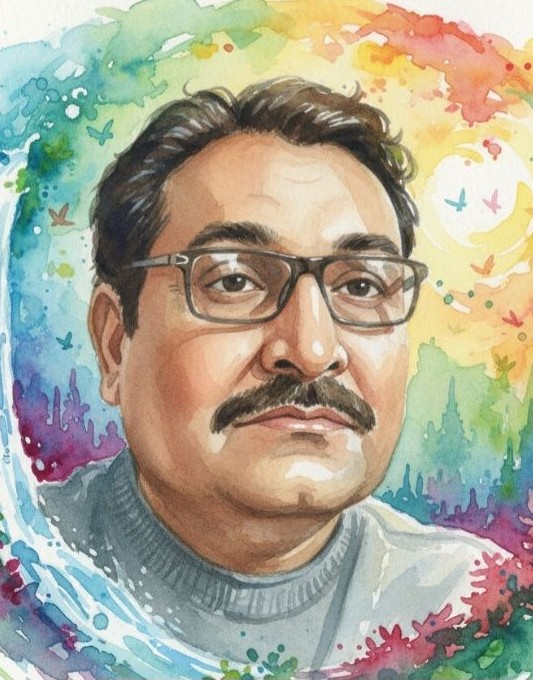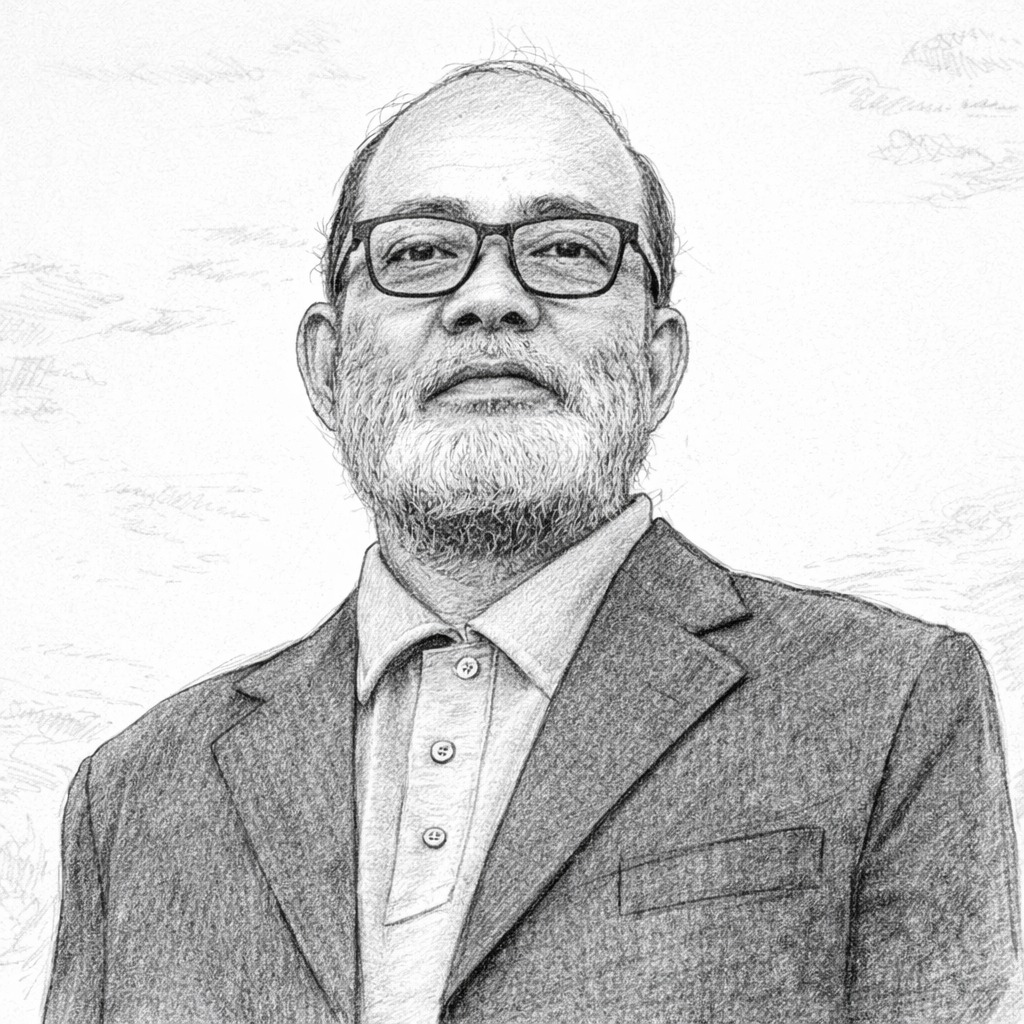কেন? – বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতি
- প্রকাশিত: শনিবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৫
- ২৬২ বার পড়া হয়েছে

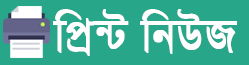
কেন? – বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতি
ইকবাল জিল্লুল মজিদ
কেন?—এই প্রশ্নটাই যেন আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতির মূল শব্দ হয়ে আছে। বাংলাদেশের যত নির্বাচন হয়েছে, তার প্রতিটি পর্বেই নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রশ্ন জাগে—কেন?
কেন নাগরিকরা অনুপস্থিত?
স্বাধীনতার পর নাগরিকের ভোটাধিকারকে কি সত্যিই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? কেন নির্বাচন মানেই শক্তিশালী প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রভাব? কেন সাধারণ মানুষকে শুধুই ভোটের দিনে দরকার হয়, তার পর তাদের মতামত ও দাবি মুছে যায় রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে? কেন নাগরিককে শোনার আগ্রহ শাসকগোষ্ঠীর নেই?
কেন নির্বাচন ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছামতো?
১৯৭৩ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারই নির্বাচনকে নিজেদের পক্ষে সাজিয়েছে। কেন তারা ভাবে, জনগণের প্রকৃত ভোটে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়? কেন তারা মনে করে, ক্ষমতা ছাড়া টিকে থাকা যায় না? কেন নির্বাচন মানে শুধু বৈধতার মোড়ক—জনগণের প্রকৃত রায় নয়? কেন তারা প্রতিবার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে দমন করে, ভীত করে, অথবা মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে একতরফা বিজয় অর্জনের চেষ্টা করে?
কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দরকার হয়?
একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন নির্বাচনের জন্য বিশেষ সরকারের প্রয়োজন হয়? কেন দলগুলো পরস্পরের ওপর আস্থা রাখতে পারে না? কেন প্রতিবার বিরোধী দল দাবি তোলে—নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না? কেন ১৯৯৬ সালের আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের জরুরি সরকার পর্যন্ত একই চক্র ঘুরে ফিরে আসে? কেন আজও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনা জনমানসে প্রাসঙ্গিক থাকে?
কেন প্রতিটি দল একই পথে?
আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সামরিক শাসন—যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, কেন শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না? কেন প্রতিটি দল প্রতিশ্রুতি দেয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার, অথচ ক্ষমতায় গিয়েই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? কেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া হয় না? কেন রাজনীতির মূল চরিত্র “নাগরিক”—কেবল দর্শক হয়ে থাকে, অভিনেতা নয়?
শেষ প্রশ্ন—কেন?
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরও কেন ভোটের দিন মানে মানুষের মনে ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস? কেন আমাদের রাজনীতি এখনো বিশ্বাস ও আস্থার সংকটে? কেন নাগরিকেরা আজও ভাবে—তাদের ভোট কি সত্যিই গণনা হয়? কেন রাষ্ট্রকে জনগণের প্রকৃত হাতে তুলে দেওয়ার সাহস কারো নেই?